The Poet, therefore, is truly the thief of fire: Arthur Rimbaud.
সেটা সম্ভবত মার্চ মাস, বাংলাদেশের একজন কবির
একটি বই আমার হাতে এল। এর আগে বিচ্ছিন্নভাবে এই কবির লেখা পড়েছি,
ভালো লেগেছে, আগ্রহ তৈরি
হয়েছে তাঁর লেখার প্রতি। কিন্তু এই প্রথম তাঁর সম্পূর্ণ একটা
বই আমার হাতে। কবির নাম জুয়েল মাজহার, বইয়ের নাম ‘নির্বাচিত কবিতা’, প্রকাশক ‘বেহুলাবাংলা’। জুয়েল মাজহারকে আমি চিনি ফেসবুকের মাধ্যমে। আর্ন্তজালের এই পৃথিবী কোনও কাঁটাতারের শাসন মানে না। ফলে এখন আমরা খুব সহজেই হদিশ পেয়ে যাই কোন দেশে কী লেখা হচ্ছে। তা সত্ত্বেও একজন কবির অন্তত কিছু বই না পড়লে তাঁকে সম্যকভাবে জানা যায় না। ফেসবুকের পাতায় জুয়েলের কবিতা নিয়মিত পড়তে পড়তে কতদিন চমকে গেছি, এক অদ্ভুত বিস্ময় আমার মধ্যে কাজ করেছে, কতদিন এক একটা কবিতা পড়ে থম মেরে বসে থেকেছি, এভাবেও
ভাবা যায়! তারপর সীমান্তের বেড়া ভেঙে এই
বইটি যখন একদিন আমার হাতে এসে পৌঁছল, সেদিন বড় আনন্দের,
প্রাপ্তির। এই কবিকে আমি সামনে থেকে দেখিনি, দেখিনি তাঁর যাপনপ্রক্রিয়া, কিন্তু কবির
সঙ্গে নিভৃত আলাপন তো হয় তাঁর কবিতার মাধ্যমেই। কবিতাই পারে একজন মানুষের ভাবজগতকে খুলে ধরতে, সেই মানুষটির জীবনবোধ ও যন্ত্রণাকে উন্মোচিত করে দিতে। তাই কবিতার জগত একটাই পৃথিবী, একটাই দেশ। তার কোনও জাতি-ধর্ম-বর্ণ বিভেদ নেই। যেটুকু আছে তা হল, স্থানিক সংস্কৃতি,
ভূগোল, ইতিহাসের ধারা, ভাষার
তারতম্য।
আগেই বলেছি, ব্যক্তি
জুয়েলকে আমি জানি না। তাঁর সঙ্গে প্রকৃত অর্থে আমার আলাপ
শুরু হয় এই বইটি পড়তে শুরু করার পর থেকেই। একজন পাঠকের সঙ্গে একজন
কবির আলাপ ঠিক যেরকম হয়, একের পর এক কবিতা পড়তে
পড়তে খুলে যায় এক অতীন্দ্রিয়-লোকের দরজার কপাট, আস্তে আস্তে প্রবেশ করতে থাকি কবির মনোজগতে। জানি না কতটা পেরেছি, কারণ, কবিতা কিছু কথা বলে, কিছু ঢাকাচাপা দেওয়া থাকে,
জানি না সেই ঢাকনা উঠিয়ে ডেকচির ভেতর ফুটতে থাকা গরম ভাতের ওম আমি কতটা
ছুঁতে পেরেছি।
এই বইটি নিয়ে লিখতে শুরু করার আগে ভেবেছিলাম, কবিকে কিছু
প্রশ্ন করব, তাঁর ব্যক্তিজীবনকে কিছুটা হলেও জেনে নেব। তারপর মনে হল, থাক না, এই
লেখা বরং হয়ে উঠুক কবিতা ও পাঠকের এক নিভৃত আলাপচারীতার দলিল। আসলে প্রত্যেক কবিরই
এক ব্যক্তিগত কবিতাজগত থাকে, থাকে এক অন্তরঙ্গ আলো অন্ধকারে নিজস্ব যাপন, যা
লুকিয়ে থাকে মোটিফ, মেটফর, শব্দখেলার মোড়কের ভেতর। সেই উজ্জ্বল মোড়ক খুলে ভাঁজে
ভাঁজে লগ্ন হয়ে থাকা বোধ, ঘাম ও রক্তকে খুঁজে নিতে পারার এই জিগস পাজল আমি কতটা
খেলতে পারি দেখাই যাক না। কবির অনিশ্চয়তা, ভয়, সাধারণ মুহূর্তের মধ্যে অনন্তকে
দেখে ফেলার, ছুঁয়ে ফেলার অংশীদার কিছুটা হলেও তো হতে পারব।
ওপেক অথচ বহুমাত্রিক ধ্রুপদীয়ানাতে জুয়েলের কবিতাভাষা
নির্মিত। বাস্তব আর পরা-বাস্তব তাঁর লেখায় হাত ধরাধরি চলে। নিছক শুয়ে বসে আয়েশ করে পড়ার মতো কবিতা তিনি লেখেন না। তিনি যেন
সেই মহাজাগতিক স্থপতি, যাঁর পথ চিরন্তন, কিন্তু নিজেই নিজের উত্তাপে গলনাংকে পৌঁছে
গিয়ে ফেটে পড়তে চাইছেন, আর উল্কাপিণ্ডের মতো সেই টুকরোগুলি পরিণত হচ্ছে এক একটি
অমোঘ কবিতায়। মেধা ও ক্লাসিক্যাল নিঃশ্বাসপতনের স্বর লেগে থাকে তাঁর কবিতায়।
কবিতার পাকঘরের আখায় জারিত হচ্ছে এক একটি শব্দ, আর ব্যালেন্সের খেলায় তুখোড় জাগলারের
মতো তিনি তৎসম শব্দের পাশে বসিয়ে দিচ্ছেন পাশ্চাত্য ভাষার শব্দ, কখনও বা কৌমসমাজের
অতিব্যহৃত শব্দগুলি শুধুমাত্র প্রয়োগের গুণে ঝলসে উঠছে ইস্পাতের ফলার মতো। যেন
শব্দ নিয়ে জুয়া খেলতে বসে প্রতি দানেই জিতে যাচ্ছেন কবি। আসলে, বাংলা কবিতায় জুয়েল
মাজহার এক অন্য স্বর। এক স্বতন্ত্র আওয়াজ। তাঁর কবিতা কখনো আমাদের নিয়ে যায় মিথ ও পুরাণের এক অতিলৌকিক জগতে, কখনও প্রকৃতির চিত্রকল্পময়তায়, আবার কখনো সমাজের কর্কশ ধ্বনিটি বেজে ওঠে দরবারি
কানাড়ায়। কৌমসমাজের ভাষা, আঞ্চলিক ডায়লেক্ট কবিতায় কীভাবে ব্যবহার করা যায় তার চূড়ান্ত উদাহরণ
জুয়েল মাজহারের কবিতা। তাঁর লেখায় শুধু এশিয় দেশগুলির দর্শন, পুরাণ, বা প্রাচীন সাহিত্যের উপাদান নয়,
বরং সমগ্র পৃথিবীর আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস, স্থানিক ও
বৌদ্ধিক চিন্তাভাবনার ছোঁয়া লেগে থাকে। এ তাঁর বিস্তৃত পড়াশোনা, মুক্ত চোখে সমাজ
ও প্রকৃতিকে দেখার ফসল।তাঁর দীর্ঘ ভবঘুরে জীবন যাপনের দাগ তাঁর কবিতার প্রতি ছত্রে
লেগে আছে। সেই সঙ্গে বাংলা ছন্দের লাগাম তাঁর
হাতে এক পোষমানা বাজপাখি।
‘নির্বাচিত কবিতা’ বইটিতে ক্রমানুসারে যে কাব্যগ্রন্থগুলির
থেকে কবিতা নেওয়া হয়েছে, সেগুলি হল, ‘দর্জিঘরে
এক রাত’, ‘মেগাস্থিনিসের হাসি’ এবং
‘দিওয়ানা জিকির’।
বইটি হাতে নিয়েই প্রথম ধাক্কা উৎসর্গ কবিতা,
ডাকবা আমারে তুমি লুকায়া লুকায়া একদিন!
যেন এক ভেকশিশু, হাইঞ্জাকালে কচুর বাগানে
ডর পায়া, চিল্লায়া, একলা মায়েরে
তার ডাকে
কে ডাকবে, কাকে ডাকবে! একটি ভেকশিশু, ধরে
নিতে পারি একটি মানবশিশুও সন্ধ্যের অন্ধকারে কচুবনে, বা এই সামাজিক
জঙ্গলে যে বিপন্নতায় চিৎকার করে তার মাকে ডাকে, সেই বিপন্নতায়
কবিকে ডাক দিচ্ছে কেউ, কে সে? সে কি কবির
ভালোবাসার মানুষ, নাকি সে কবিতা, কবিকে
তাঁর মর্মমূল ধরে টান দিচ্ছে। মা শব্দটাই
এত অমোঘ একটি শিশুর জীবনে, যে, যা কিছু ভয়,
ভালোবাসা, রাগ সবেরই আদানপ্রদান এই মায়ের সঙ্গেই। আর শিশুবয়েস পেরিয়ে এসেও ভয় পাওয়ার মুহূর্তে, ব্যথা পাওয়ার মুহূর্তে মানুষ কিন্তু সবার আগে মাকেই ডাকে। আর এই সঙ্গে আমাকে বিস্মিত করে গ্রামীণ
কৌম সমাজের ভাষার এই সাবলীল ব্যবহার। সাহিত্যের
ভাষার যে প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত নিয়ম, তাকে ভেঙে এইভাবে জুয়েলের
কবিতা প্রথমেই আমাদের হৃদয়ে এসে ধাক্কা দেয়। এ যেন এক সহজিয়া সাধকের ভাষা। একটি মানুষের সঙ্গে আরেকটি মানুষের বিনিময়ের
ভাষা, যেখানে সাজানো গোছানো কিছু নেই। যা কিছু স্বতঃস্ফুর্ত, তাই কবিতা হয়ে উঠেছে।
‘দর্জিঘরে এক রাত’ কবিতায় তাই দর্জিমহল বলে কবি এই সম্পূর্ণ
সমাজকেই অভিহিত করেন। যে সমাজের
বুকে বিঁধে আছে শূন্যতা নামের এক বল্লম। জুয়েল
এখানে এক নীরব দর্শক, যখন ‘লক্ষ শিশ্ন হাতে
চেপে দর্জিদল’ মেঘের দিকে দৌড়ে যাচ্ছে, এই দীর্ঘ অবসরে তিনি আতশ কাচের গুঁড়ো দিয়ে ঢেকে দিচ্ছেন ‘ফাঁকফুঁক, দর্জিঘর, ঘড়ি ও জানালা’। একি সমাজের ফাঁকফোকর ঢেকে দেওয়ার ইঙ্গিত! ঘড়ি শব্দটির ব্যবহার বারবার পাই জুয়েলের কবিতায়। আপাতসময়কে ঢেকে দিয়ে তিনি কি কোনও মহাসময়ের
কথা বলতে চান? আরও বিস্মিত করে ‘দশবস্ত্রে-দিগম্বর’ শব্দবন্ধ। এখানে যেন ভোগবাদের নির্লজ্জতাকে কবি আরও নগ্ন করে
তুলেছেন।
‘ভয় বুঝি সংবেদনের কোনো ডানা?’ আহা, এই উচ্চারণ কবিকে স্বতন্ত্র করে তোলে, পাঠকের চেতনাজগত
টাল খেয়ে যায়। ‘ক্রমহননের পথে’
রিরংসা নামের এক বিস্ফোরণের ভয়। আর এই ভয় থেকে সরে আসতে চেয়ে কবি উড়াল দিতে চান, এই শ্লথ মৃত্যুউপত্যকা পাড়ি দিয়ে ঘাসের চলমান সিঁড়ি বেয়ে এক আশ্চর্য অরণ্যে,
যেখানে মনুষ্যখুলির ছায়া প্ররোচনার মতো সাজানো রয়েছে পর্বতের ধাপে ধাপে। আসলে কবি পাড়ি দিচ্ছেন না এই পথ, কবিকে জড়িয়ে সাপটে ধরে তাঁরই ওপর ঝুঁকে আছে এই ক্রমহননের পথ। একে কী মৃত্যুচেতনা বলবো, আত্মক্ষয়!
আবারও ফিরে আসি, যতবার এই বই পড়তে নিয়েছি, বারবার ফিরে এসেছি এই পংক্তিগুলোর
কাছে,
নিঃশব্দ কামানে তুমি একা বসে ভরছো বারুদ।
শীতকাল গেল;
নিঃশব্দ কামানে তুমি একা কেন
ভরছো বারুদ?
(মেগাস্থিনিসের হাসি)
এখানে তুমি বলতে
কি জুয়েল নিজেকেই বুঝিয়েছেন? আমার মনে হয়, হ্যাঁ। আর বুকের
ভেতর রিনরিন করে এক ব্যথা বেজে ওঠে। এক শীতল যন্ত্রণা। যেন এক বুড়ো, এক অতিবুড়ো কামান, যার কোনও সাড় নেই, নেই কোনও সংবেদনশীলতা, হতে পারে সে জীবনে এসে পড়া কোনও
মানুষ, হতে পারে কবির নারী, আবার হতে পারে
এই জড়সদৃশ সমাজ, তাতে যতই ঠুসে বারুদ ভরা যাক না কেন,
সে আজীবন মূক ও বধিরই থেকে যাবে। এইখানে বহুমাত্রিক হয়ে ওঠে জুয়েলের কবিতা। বলা ও না বলা কথার এক ছায়াময় পাণ্ডুলিপি
যেন। আর এই শক্তিচালিত তামাশার মধ্যে কি শোনা
যায়? এঞ্জিনের শব্দ আর রোবটের কাশি। স্তম্ভিত হয়ে যাই যখন যন্ত্রসভ্যতার প্রতি মৃদু শ্লেষের
আপাত আড়ালে আরও গভীর কোনও দর্শনের খোঁজ পাই, যখন শেষ লাইনে এসে জুয়েল
বলেন,
নিঃশব্দ কামানে তুমি এখনো কি ভরছো বারুদ?
তারপরেই ‘দশ পায়ে নাচি’ কবিতায় আবার দেখি
সামনে খুঁজি তাকে, পেছনে তাকাই
ঘুমের পোশাক গায়ে দশ পায়ে নাচি
ঘুমের পোশাক
গায়ে বলতে জুয়েল কি প্রকৃত ঘুমের কথা বলেছেন, স্বপ্নের কথা? হয়তো না। এ হল কবির
সেই ঘোর, সেই ট্রান্স, যা তাকে দিব্যদৃষ্টি দেয়, আলাদা করে ফেলে আর পাঁচজন মানুষের
থেকে। কবি বিপন্ন হয়ে খুঁজছেন, কাকে খুঁজছেন, কে সে?
ঘোড়া ফেলে দিচ্ছে আমাকে আর তার জিন;
তবু বাতাস এক ঘোড়া
সে ছুটছে আমাকে নিয়ে
……………………………
পথের ক্লান্তিহেতু গ’লে যাচ্ছে খুর
আমার ঘোড়ার;
আমার হৃদয় আজ ঝুলছে অনেক ডালে ডালে
(দশ পায়ে নাচি)
ঘোড়া শব্দটিও জুয়েলের কবিতায় ফিরে ফিরে এসেছে। হয়তো ভ্রমণ, হয়তো বোহেমিয়ানিজম তাঁর জীবনের এক
অন্তরঙ্গ আত্মা, তাই এই গতির কথা, অথবা
সময়ের দৌড় বারবার সংক্রামিত করেছে তাঁকে। ছুটতে ছুটতে গলে যাচ্ছে ঘোড়ার খুর। একটা ছবি ভেসে উঠছে পাঠকের সামনে। বাতাস বলি, ঘোড়া বলি, যাই
বলি না কেন, মনে হছে দূর দিকচক্রবালে মিলিয়ে যাচ্ছে সময়ের ধুলো,
ঘোড়ার গলে যাওয়া খুর। হৃদয় আজ ঝুলছে অনেক
ডালে ডালে, সালভাদোর দালির সেই বিখ্যাত ছবি মনে করিয়ে দেয়। যখন কবি বলছেন,
রাত্রির উপসংহার এলিয়ে পড়ছে মোরগঝুঁটিতে
তার শিরদাঁড়া বেয়ে নামছে রক্তঘন চিৎকারের নদী
এক অন্যস্বাদের ভোরের
ছবি এঁকে দেন কবি। সে ভোর অসহায়তার, সে ভোর চিৎকার দিয়ে ঘেরা। ‘মহাবাতাসের ফেনা’
কবিতাটা একটু পড়ে দেখা যাক,
নিষ্পাদপ প্রান্তরের পথে পথে নতমুখ ঘোড়া
মহাবাতাসের ফেনা লেগে আছে তাদের কেশরে
...........................................................................
অদূরেই হানাবাড়ি; হেঁটমুণ্ড প্রেতিনীরা দল বেঁধে তাতে বাস
করে;
তাদের উনুন আজ ঘোড়াদের লাল মাংস চায়
..............................................................................
এমনকি আবহকুক্কুট তারও পক্ষপাত
অনন্ত ঘুমের দিকে, বিভ্রমের দিকে
এই কবিতার ভাঁজে ভাঁজে মিথের রহস্যময়তা খেলা করে। হাওয়ামোরগের বদলে আবহকুক্কুট শব্দটি আমাকে চমকে দেয়। ঘোড়ার কেশরে মহাবাতাসের ফেনা লেগে গেলে, সে
তখন আর জাগতিক কোনও অশ্ব নয়, সে তখন মহাকালের রথের ঘোড়া। যেন তার খুরে লেগে আছে সময়ের ধুলো। প্রেতিনীদের অনুষঙ্গ মনে করিয়ে দেয়
ম্যাকবেথের সেই ভবিষ্যৎদৃষ্টা ডাইনিদের কথা, যারা
সময়ের প্রতিভূ। কিন্তু তার পরই ভুল ভাঙে, এরা শুধুমাত্র সেই ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ডাইনি নয়, আমাদের পুরাণ, লোকগল্প থেকে উঠে আসা কিছু চরিত্র নড়াচড়া
করে কবিতার শরীরে।
ঘোড়াবাগানের মধ্যে যারা একদিন দেখেছিল দৌড়
তাদের হাতের তালি শুষে নেয় প্রান্তরের বালি;
তাদের ঘুমের মধ্যে উড়ে আসে অচেনা কার্পাস।
-এতো যে কার্পাস সে তো উদ্বেগের
যুদ্ধের আতঙ্ক বুঝি কার্পাসেরই মতো ভেসে আসে
এখানে এসেই মিথ ও পুরাণের গণ্ডি ভেঙে কবিতাটি
সমকালকে ছুঁয়ে ফেলে। যে সময় যুদ্ধ, সন্ত্রাস, মহামারীর ভারে ঝুঁকে আছে। ভ্রমণের ভাষা কবিতায় এক অনন্ত ভ্রমণের ইঙ্গিত খুঁজে পাই। যেন কবির যাপিত জীবন, ভ্রাম্যমাণ জীবনের ধুলোবালি,
খড়কুটো পড়ে আছে কবিতার শরীরে।
আর একে একে দূরের পাহাড়ে
শান্ত, নীরব জেব্রারা ঝরে যায়
আফ্রিকার এক বনাঞ্চলের
ছবি দেখতে দেখতে এইখানে এসে এক প্রতিবাদহীন ঝরে যাওয়া, হেমন্তের অরণ্যে খসে পড়া পাতাদের মতো একে একে নিভে যাওয়া। এই জেব্রারা যেন সমাজের পিছিয়ে পড়া শোষিত মানুষের প্রতিনিধি, বিনা প্রতিবাদে নিভে যাওয়াই যাদের
নিয়তি।
‘মধুব্রজনের জ্যামিতি’ কবিতার নামটিই চমকপ্রদ। জুয়েলের শব্দ ব্যবহারের নৈপুণ্য এবং পরিমিতিবোধ বারবার পাঠককে এক নতুন অভিজ্ঞতার
দিকে ঠেলে দেয়। পাঠক ধাক্কা খায়, তার চিরাচরিত পাঠাভ্যাস, তার শব্দ ও বাক্যের
ধারণা ধাক্কা খায়। এই কবিতাটিও তার ব্যতিক্রম
নয়। ‘উৎপ্রেক্ষার বাড়ি’,
‘উপমার গিরিখাতে’, ‘অনুপ্রাসের মতো বয়ে গেছে পর্বতচূড়া’,
‘ব্যজস্তুতির বাঘ’, এই শব্দবন্ধগুলি বাংলা কবিতার
চলমান ধারায় উজ্জ্বল ধুমকেতুর মতো ছটা বিচ্ছুরিত করে বেঁচে থাকবে।
বইয়ের কবিপরিচিতিতে দেখি অর্ক মাজহার
তাঁর পুত্রের নাম। ‘কুব্জপিঠ স্বাপ্নিকের হাসি’ কবিতাটি
পড়ে প্রথম সন্তানের মুখ দেখার পর পিতার অনুভূতির এক টুকরো ঝলক আমরাও
ভাগ করে নিতে পারি আমাদের সেই দিনটির সঙ্গে,
নয়টা এক মিনিটে
হাসপাতালে পুত্র আনে সমুদ্রঝলক।
আয়না কাঁপিয়ে হাসে শাদা-রেশমি
কাপড়ে জড়ানো গাছপালা!
‘সাধুবচনের ভার’ কবিতায় জুয়েল লেখেন,
কেননা সে প্রসারণক্ষম, কেননা সে স্প্রিং
প্রসারণক্ষম-এর পরেই
স্প্রিং শব্দটি বসানোর জন্য যে ধক লাগে, তা জুয়েলের কলম বারবার
প্রমাণ করেছে। বাক্যকে আলপিনের মতো সূক্ষ্ম, অথচ ধারালো করে তোলার জাদু এই কবির হাতে আছে। তাই তিনি অনায়াসে পথকে ঠাণ্ডা, শক্ত
ঘুমন্ত একটা কামানের সঙ্গে তুলনা করতে পারেন। কল্পনাশক্তি, উপমা ও চিত্রকল্পের এক
চূড়ান্ত উদাহরণ জুয়েল মাজহারের কবিতা। হোসপাইপের ঘটনা ভুলে কবি পরখ করে নেন নিজেদের পেন্ডুলাম।ততক্ষণে বিশেষ্যের খোকা ঘুমিয়ে পড়েছে
বিশেষণের বাঁকা ডালে, আর কবির মনে পড়ে যাচ্ছে,
একদিন তাঁরই ঘ্রাণে লাল হয়ে উঠেছিল মেয়েলি অব্যয়। জলের আঙুলে আঁকা চিত্রময় শুয়ে থাকে কবির নারী। আর ক্রমহননের পথ কবিকে জড়িয়ে নিয়ে ঝুঁকে থাকে সেই নারীর ওপর।
‘রক্ত-সম্পর্ক’
কবিতাটি একবার পড়ে দেখা যাক,
বসন্ত সরাইয়ের পথ পাড়ি দিতে দেখেছিলাম
দু’জন হোমোসেপিয়ান তাদের হোসপাইপ
ছেড়ে দিয়ে হাসছে
এতে ভিজে যাচ্ছিল সবার গা
আর, আমার সদ্য ঋতুবদল-করে-আনা মন
সমস্ত ঘটনার সঙ্গে সম্পর্ক মূলত ক্রিয়া ও অব্যয়ের;
তাদেরই তা’য়ে বড় হয়ে ওঠে যৌথ মমতার কোকিল
হোমোসেপিয়ানস,
হোসপাইপ, হাসছে, এই তিনটে শব্দ পরপর বসানোর জন্য কিন্তু সাহস লাগে, আর সেই সাহসের
প্রমাণ বারবার পাই জুয়েলের কবিতায়। কোথাও এতটুকু মোনোটনি আসেনি এরকমভাবে শব্দ
ব্যবহারে, বরং এক আশ্চর্য পারম্পর্য তৈরি হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে ক্রিয়া ও অব্যয়ের
যোগাযোগের মিথস্ক্রিয়াকে বর্ণনা করতে গিয়ে কোথাও এতটুকু যান্ত্রিক বা বিবৃতিমূলক
হয়ে ওঠেনি তাঁর কবিতা।
ঘড়ির তিনটে কাঁটা চুপিচুপি
উড়াল দিয়েছে, কখন? যখন আলস্যে
উবুড় হয়ে মদালস ঘড়ি শুয়ে ছিল। আর আমরা ঢুকে যাই অনন্তের রহস্যে। ঘড়ির ঘুম ভাঙে। সময়ের ইতিহাস তখন আর ঘড়ি জানে না। ঘড়ির তিনটে কাঁটা এসে ফের ঘড়িতে বসেছে। ‘চন্দ্রজাল ১’
কবিতাটি পড়তে পড়তে গায়ে কাঁটা দেয়, এভাবেও
ভাবা যায়, উপস্থাপন করা যায়! আবার একই কবিতার দ্বিতীয় অংশটি
পড়তে গিয়ে চমকে উঠি,
‘সহসা ভেঙেছে ঘুম পিরিচের মতো খানখান’
..............................................................................
শিথানে-পৈথানে প্রেতস্বর
.................................................................................
বত্রিশ দাঁতের পাটি খুলে হাসে একশো করোটি
আমুণ্ডু ভয়ের সাপ লোল জিভে চাটছে আমাকে
.................................................................................
স্ট্রাটোস্ফিয়ার ছেড়ে উড়ে যাচ্ছে ধ্রুপদ বেলুন
আমার শরীরে সাপ, কূটজাল, ভয়ের করাত!
এই মহাবিশ্বের
বায়ুস্তর ছেড়ে উড়ে যাচ্ছে ধ্রুপদ বেলুন। প্রথমেই চমকে যাই বেলুন শব্দটির আগে
ধ্রুপদ শব্দটিকে দেখে। এখানে কী ধ্রুপদ গানের মতো ধীর লয়ে বেলুন উড়ে যাওয়ার কথা
বলছেন কবি, নাকি স্থির এক বেলুন, যা বায়ুজীবি, সে উড়ে যাচ্ছে বায়ুস্তর ছাড়িয়ে! সে
কি মৃত্যুর দিকে চলে যাচ্ছে ধীরে ধীরে, আর সেই ভয়ের করাত নিরন্তর কেটে টুকরো টুকরো
করছে কবিকে? কবি কি এখানে এক চাঁদগ্রস্ত উন্মাদ? চাঁদ কি কবির প্রেমিকার প্রতীক?
হয়তো হ্যাঁ, আবার যখন দেখি একমাথা কালো চুল ভয়ের হুলের মতো খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে,
ভীত সন্ত্রস্ত কবি দুই হাতে শিশ্ন ঢেকে বসে থাকেন মাটিতে, তখন মনে হয়, না, জুয়েল
আর পাঁচজনের মতো শুধু চাঁদের সৌন্দর্য্য-মুগ্ধ প্রেমিক নন। তিনি যেন এক দগ্ধ
কাপালিক, গিলে খাচ্ছেন চাঁদের সুরুয়া। তাঁর এক হাতে উপুড়করা চন্দ্রদুধের বাটি আর
হেঁতালের লাঠি, অন্যহাতে সদ্যমৃত মানুষের কঙ্কাল, অথচ চোখে স্বপ্নমায়াজাল। নাঙ্গা
কৃপাণ, হাড়ের মালায় তিনি এক শুদ্ধ তন্ত্রাচারী, তাঁর শরীরে সাপ, এখানে কি
কুলকুণ্ডলিণীর ইঙ্গিত দিয়েছেন কবি!
এখানে পাথরগুলো কী নরম স্পঞ্জে বানানো!
সেদ্ধ ডিমের মতো ডাঁসা ও বর্তুল;
তাতে আমি টের পাই আঁচ। টের পাই
অপার্থিব দোলা ও স্পন্দন।
..................................................................
কামিনীফুলের ঘ্রাণ বুকে নিয়ে ভেসে যাবে প্রস্রবণে
-আরো দূরে তপ্ত, গাঢ় লবণ-সাগরে।
(আরোহণ)
নারী-পুরুষের
শারীরিক সম্পর্কের বর্ণনার জন্য কবিকে কোনও যৌনতা-প্রবণ শব্দ ব্যবহার করতে হয় না।
এখানেই চরম সার্থকতার সঙ্গে কবিতা ফুটে ওঠে। ঝড়-ঝঞ্ঝা, হাওয়ার চাবুক সয়ে তাকে তার
মোক্ষে যেতে হবে। কবিতার মোক্ষ বোধহয় একেই বলে।
বেশ কয়েকটি দীর্ঘ
কবিতা আছে এই বইতে। তাতে কিছু গল্পের ইঙ্গিতও আছে, কিন্তু তার জন্য কাব্যধর্মীতা
ব্যাহত হয়নি। যেমন ধরা যাক ‘চাঁদে পাওয়া গাধা ও উজবুক’ লেখাটি ছ’পাতার এক কবিতা,
অথচ একটানে পড়ে ফেলা যায়। এখানে ছন্দের এক অনন্য খেলা আছে, আছে এক অনন্ত
ভ্রাম্যমাণতা, এ যেন শব্দে শব্দে বোনা এক নকশিকাঁথা, যা জুয়েলের স্বকীয়তা। একটু
পড়ে দেখা যাক,
ঘুরছি দিশেহারা
চাঁদের রাস্তায়
বক্র ঘেরাটোপে
একাকী মিনোতার;
-সস্তা হোটেলের
করুণ খদ্দের
...................................................
চাঁদের নীচে আর
আকাশগঙ্গায়
জাহাজ ভাসাবার
আঁটছি ফন্দি;
-আপাদমস্তক আদার ব্যাপারী
........................................................
স্বপ্নে উপহার
পেয়েছি গাধাটিরে
নিজের মুকুরেই
পেয়েছি একে আমি
...............................................................
শর্ত একটাই!
শিশুর মতো
এই
অবুঝ
শিশ্নকে
পাড়াতে হবে ঘুম;
রাখতে হবে একে
ত্বকের খাপে ভরে
[ও বড়ো বেয়াড়া, অনেক আবদার!]
..............................................................................।।
কিন্তু এ কী তুমি হঠাৎ মরীচিকা!
আমায় একা ফেলে কোথায় কই গেলে
স্বপ্নসম্ভব চতুষ্পদ?
........................................................................
আমায় ঘিরে আজ আগুন গ্লেসিয়ার
ভল্ল পশুপত ছায়ার অশরীরী;
পত্রমোচী গাছ ঝরায় ভয়পাতা
.......................................
হে মাতঃ বঙ্গ তাপিত অঙ্গ
বক্ষে তব আজ দাসেরে ঠাঁই দাও
...............................................................
ফিরিয়ে নাও মোরে
এ হেন
কীটাণুরে
তোমার জরায়ুর
অশেষ নির্ঝরে
নিজের প্রতি শ্লেষ,
ব্যাঙ্গ, কৌতুক এবং সর্বোপরি এক বিষম নিরাপত্তাহীনতার ধারাভাষ্য এই কবিতার কবি
কিন্তু শেষ অব্দি গিয়ে আশ্রয় চাইছেন তাঁর মাতৃভূমি, তাঁর বঙ্গভূমির জরায়ুর
অন্ধকারে। এইখানে এসে আমার কেন জানি না মাইকেল মধুসূদন দত্তকে মনে পড়ে গেল।
তাঁর তীব্র
পুরুষালি করালভৈরবের মতো উচ্চারণের মাঝেও কখনও কখনও খুঁজে পাই এক নম্র পেলব
মানুষকে, যে তার ক্ষুৎকাতর পিঁপড়েদের ডেকে বলছে,
নাও, এই নিবিড় রোদনভরা গাছ
এই করুণ ফলসা পেড়ে বসন্তের দিনে
এর রসে ভেজাও ঠোঁট, কাতর করো একে;
এখানে প্রেমিক
জুয়েল তাঁর গানপাগল মেয়ে-কোকিলের দুঃখে দুখি, তাই সেই গান থামে না, যতই ভূশণ্ডির
কাক তার বুকের তন্ত্রী ছিঁড়ে গানের কলি ঠুকরে খাক না কেন, মরা কোকিল আবার গান গায়,
গান গায় চিরকালের বনে।
একটা প্রবন্ধে
জুয়েল লিখেছেন,
“সত্তুর দশকের মাঝামাঝিতে বাড়ি
ছেড়ে পালিয়েছিলাম। কখনো আর সেভাবে বাড়িফেরা হয় নি। স্টেশনে স্টেশনে ঘুরে, প্ল্যাটফর্মের বেঞ্চিতে ঘুমিয়ে, আজ এর কাল ওর বাড়িতে
আশ্রয় নিয়ে, কখনো লজিং থেকে, তারপর
আবারও দূরের কোনো গ্রামে-শহরে ‘আজনবি’ হ’য়ে হাজির হওয়াটা ছিল অভ্যাস; সেইসঙ্গে ললাটলিখনও।
এরই মধ্যে ১৯৮২ সালে মৌলভীবাজার সরকারি কলেজে ভর্তি হবার পর বলা-যাবে-না-এমন এক
কারণে আমি আর সহপাঠী আবদুল ওয়াহিদ (যে এখন নিজ এলাকার এক স্কুলের হেডমাস্টার মশাই)
শহর থেকে মাইল পাঁচেক দূরের গা-ছমছম কালেঙ্গা পাহাড়ের দুর্গম গভীরে ঠাঁই
গেড়েছিলাম। শহরে যেতাম দীর্ঘ পথ হেঁটে সকালে। ফিরতাম রাতে,
কখনো-কখনো অনেক রাতে; কখনো বৃষ্টির অত্যাচার সয়ে
বা চাঁদকে মাথায় করে গভীর অরণ্যের ভেতর দিয়ে আমাদের বন্য ডেরায়।“
আমার জানা নেই কেন তিনি
বাড়ি থেকে পালিয়েছিলেন। কিন্তু জুয়েলের লেখা পড়তে পড়তে মনে হয়েছে, তিনি যেন এক
জন্ম-বাউদিয়া। তাঁর ডানায় ভ্রমণের গন্ধ লেগে আছে। তথাকথিত সভ্য সমাজ থেকে বারবার
পালিয়ে যেতে চেয়েছেন কবি জুয়েল মাজহার।
নিজেকে সরিয়ে দূরে, আলগোছে
গাছের গোপন কোনো ডালে রেখে
আসি;
নানা রকমের হাওয়া,
রোদবৃষ্টি হিম-কুয়াশায়
পাখি এসে ঠোকরায়। ভাবে;
পেয়েছি কেমন ফল। বোঁটকা-ঘ্রাণ।
তবু কাছে টানে!
তাই তো নিজেকে ঘুমন্ত রেখে
এখনও ছায়ারূপে তিনি বেরিয়ে পড়েন সূর্যহীন কান্তারের পথে, পতনশীল হিমবাহের ভেতর
দিয়ে তাঁর নৌকা চলতেই থাকে অবিরাম। তিনি এক নিষেধ না মানা মাছ, সবার অলক্ষ্যে ভেসে
চলেন। সমুদ্রযোনির গর্ভে তিনি যেন এক মন্ত্রপূত শুশুকের ভ্রূণ।
তাকে ডাকে উত্তমাশা
অন্তরীপ
আর ঘন নীল আসমান;
-ডাকে আমাকেও;
তার গর্ভে থাকি আমি
সে আমার ভেতরে বাঙময়;
তিনি বিমূঢ় বিব্রত, তবুও
তিনি বিহসিত নীলে আত্মহারা। এমনই এক আশ্চর্য কবি জুয়েল। তাঁর কাছে রাত্রি এক ঘন
আত্মরতি। সর্প আর বৃশ্চিকের ভাবাশ্রয়ে তাঁর বেলা কেটে যায়। আবার চান্নিপসর রাতে,
মন উদাস করা বাতাসের ভেতর অন্ধ গলি আচমকা ফকফকা শাদা হয়ে ওঠে তাঁর কবিতায়। কে এই
কেরামত? কেরামত নাকি জুয়েল, জুয়েল নাকি কেরামত, তার রিকশা সেই রাত্তিরে চাকা ছাড়াই
একা একা মাতাল হয়ে ওঠে, যেন এক ‘জোয়ান লৌড়ের টাট্টু’। ‘রিকশার গতরে খালি ফাল পাড়ে
আলগা মর্দামি।‘
‘চান্নিপশর রাইতের লৌড়’
কবিতাটি প্রচলিত কবিতা-ধারণা, কবিতা-ভাষায় এক সাইক্লোনের মতো ধাক্কা দেয়। মূলত
উত্তর-পূর্ব বাংলার কথ্যভাষার সঙ্গে এই কবিতায় এসে গেছে আরও অন্যান্য অনেক স্থানীয়
শব্দ, এমনকী বেশ কিছু বিদেশি শব্দও। তাঁর দীর্ঘ ভবঘুরে জীবনের অভিজ্ঞতার ছাপ এই
ভাষায়। গল্প বলার চলনে লেখা এই কবিতাটিতে জুয়েল এক জাদু-বাস্তবতার জগত তৈরি
করেছেন। কবিতাটি পড়তে গিয়ে যেন এক
চলচ্ছবির মধ্যে ঢুকে যাই, যেখনে স্বপ্ন বোনা হচ্ছে নিপুণ কলমে। আবার পাশাপাশি উঠে
এসেছে সাধারণ মানুষের জীবনের চালচিত্র, তাদের বেঁচে থাকার ক্রাইসিস। ক্রাইসিস তো
থাকবেই, তবুও মানুষ স্বপ্ন দেখে, এক আশ্চর্য উড়ালের স্বপ্ন। কেরামত
এক আজব শিল্পী, যাকে সকলে “আর্টিস্ট সাব” বলে ডাকে। এই উন্মাদ শিল্পী তার খানদানি
হাতে বড় মহব্বত মিশিয়ে ছবি আঁকে রিকশার পেছনে। তার হৃদয় ফাগলাগা, সেখানে
তেলেসমাতির কারবার, মখলুকাতের সকল সুন্দর নৌকার ছবি তার হৃদয়ের জমিনে আঁকা।
কেরামত বহুত যতনে আঁকে
আজগুবি ছবি বেশুমার
সেই ছবির জমিন জুইড়া
গাছপালা নাও-নদী, পশুপঙ্খী,
লায়লা-মজনু, শিরি-ফরহাদ,
ভাল্লুক-উল্লুক সব, বান্দর-উন্দর হনুমান
ডানাঅলা বোরবাক, পঙ্খীরাজ,
ঘোড়া, জিনপরি
ছিনেমার নায়িকা মৌছুমী আর
পপি-ছাবনুর
ফুল-পাতা আসমানের চান ও
সিতারা।
আর সেই ছবি দেখে কবির মনে
হচ্ছে, ‘ওরা সব বোবার লাহান’ বসে বসে পৃথিবী ও আকাশের আন্ধাউন্ধা তামাম খেল দেখে
যায়। সেই লিলুয়া বাতাসে রিকশা যেন আর রিকশা নয়, এক পঙ্খীরাজ ঘোড়ার মতো উড়ে যেতে
চায়, যেন কেরামতকেও উড়িয়ে নিয়ে যেতে চায় এক অলৌকিক দেশে। আর এই চান্নি-পশর রাতে
কোমলাঙ্গী সুন্দরী পরিরা রিকশার গতরে শুধু সুগন্ধি ছেটায়। রাত যেন এক সমুদ্র, যার
দিলের কপাট চাবি ছাড়াই খুলে যাচ্ছে আলিশান সব ঢেউয়ের ধাক্কায়। চন্দ্রাহত কেরামত
এবং চন্দ্রাহত কবি দুজনেই তখন এক স্বপ্নের বলয়ে ঢুকে যান, দুজনেই তখন ‘এক আউলা
চান্দি, ইস্কুরুপ ঢিলা’। আর এই কবিতা পড়তে পড়তে পাঠকেরও হৃদয়ে চাঁদ লাগে, শুরু হয়
নানান রঙের তেলেসমাতির খেলা। আবার শেষের দিকে এসে এক অদ্ভুত দ্বিধা, এক অদ্ভুত
দোলাচল,
মোরজ্বালা! এইটা খোয়াব না
খোয়াবের
মাঞ্জামারা আজগুবি ঘুড্ডি
একখান
-জানে কোন হউরের পুত
স্বপ্ন ভেঙে যায়। চিপা
গলির ভেতর থেকে জীবনের গন্ধ তাড়া করে আসে, ঘাউড়া কুত্তার নাহাল খামাখা চিক্কুর
পাড়ে, পেছন পেছন দৌড়ায়।
‘দিওয়ানা জিকির’ বইটির
প্রথম কবিতায় এসে কবি যেন কিছুটা ক্লান্ত, পশ্চিমের এলানো বিকেলে সূর্যের থেকে
বহূদূরে। দীর্ঘ যাত্রার পর জাহাজ যেমন নোঙর ফেলতে চায়, তেমনই জুয়েলও যেন এবার থিতু
হতে চাইছেন, কিন্তু শেষ দুটো লাইনে গিয়ে আবার বিস্ময়, জাহাজডুবির পর যেমন নিঃশব্দ
বুদ্বুদ জেগে ওঠে, ঠিক তেমনই বিষণ্ণ ও একা তার পথ চলা।
কবি এক শব্দচাষি। আবার
‘শীতের দৈত্য’ কবিতায় সেই কবিই ভৈরবে মেঘনার তীরে বাদাম ফলান, শাদা বালির ভেতর হাত
গলিয়ে তুলে আনেন বীজের স্নেহ। মাছ এবং তাদের সম্ভাবনাময় তরুণ ডিমগুলিকে তিনি উপহার
হিসেবে পাঠিয়ে দেন রিরংসাঘন শহরের ঠিকানায়। শহরের ভোগবাদ আর জৌলুসভরা জীবন, যেখানে
কোনও সোঁদা মাটির স্পর্শ নেই, নেই কোনও আন্তরিক আলিঙ্গন, সবটাই মেকি ও সাজানো,
এমনকী করমর্দনের উষ্ণতাগুলিও সেখানে ঠান্ডা-হিম ঘুমন্ত কামানের মতো পরে থাকে, ছেঁড়া
ও পুরনো তাঁবুর ভেতর প্রেম সেখানে মৃত্যুর ঢেউ দিয়ে ঘেরা, এসবই কষ্ট দেয় কবিকে।
তিনি এক দূরের ধস্ত, মলিন মফস্বলে বসে ভাবেন, রাত্রির অসংখ্য মরানদী উজিয়ে ভাবেন,
স্মৃতি-ভস্মের ধু-ধু
প্রান্তর পেরিয়ে
বিপুল দামামাসহ আমি আবার
এক শীত থেকে অন্য শীতে
তোমার ক্রূর সৈন্যদলের
পেছনে দৌড়াবো
(শীতের দৈত্য)
এই কবিতার শেষে কোনও
যতিচিহ্ন নেই। কেননা এই দৌড় এক অনন্ত দৌড়, সৈন্যদলের বিরুদ্ধে, যুদ্ধের বিরুদ্ধে,
হননের বিরুদ্ধে কবির ছুটে চলা।
নারী ও প্রেম জুয়েলের
কবিতায় ফিরে ফিরে এসেছে। প্রেমের ক্ষেত্রে কখনও তিনি চণ্ড-ভৈরব, কখনও সমর্পিতপ্রাণ
কাতর প্রেমিক।
নারীমাছ, তোমাকে আতশকাচ
কিনে দিতে চলেছি বিদেশে
দূর কোনো সরোবর থেকে তুমি
কানকো নেড়ে চাহিদা জানাও
(ভ্রমণ)
প্রেমিকার জন্য তিনি কৌটোয়
অম্লতা ও ক্ষার নিয়ে চলেছেন নিরুদ্দেশে, টলোমলো জাহাজের প্রায় হেঁটে যাচ্ছেন
রক্তমাখা পথে। গোলকধাঁধায় ঘুরে মরছেন। এভাবে পথের বর্ণনা করতে করতে তিনি পথ ও
গন্তব্যকে যেন মিলিয়ে দিয়েছেন। হাঙর-চোয়াল বলতে কী তিনি প্রকৃত হাঙরের কথা বলেছেন!
মনে হয় আগ্রাসী এক প্রেম, যাকে ভয় করে অথচ অমোঘ তার টান কিছুতেই এড়ানো যায় না,
সেইখানে ‘লবণের অনুপ্রাসে’ তাঁর বিছানা পাতা,
দিনশেষে আনি দোলা তোমার
শয্যায়।
আমাকে দোলাও তুমি অপরূপ
রকিং ক্র্যাডেলে
আরেকটু এগিয়ে যাই কবিতার
পথ ধরে, দেখবো, কবি বলছেন, একদিন ভস্মনদীর তীরে ফের দেখা হবে, দেখা হবে ঢলে পরা
সূর্যের গ্রীবার আড়ালে, নরকের খরজলে দেখা হবে সাঁতার পোশাকে। প্রেম নিয়ে এক অদ্ভুত
দোলাচল, এক অপরূপ আকর্ষণ-বিকর্ষণের খেলা জুয়েলের মনোজগতে চলতেই থাকে। বরং বলা যায়,
প্রেম ও অপ্রেম, ভালোবাসা ও ঘৃণা, কাম ও সন্ন্যাসের সুতোয় জট লাগা, জট খোলার এক
অদ্ভুত রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটমান বর্তমান হয়ে বিরাজ করে তাঁর লেখায়। তাই জুয়েল লিখে
ফেলেন এই কবিতাটি,
বাঘিনী আমাকে শুধু ডেকে
চলে ভরা পূর্ণিমায়;
বারবার কাতর মিনতি করে আমি
তারে বলিঃ
দয়া করো, আমায় খেয়ো না,
আমি
অসহায় অতি ছোটো জীব
প্রেম থেকে, বাঘিনীর
অতিরিক্ত রতি-আক্রমণ থেকে পালিয়ে আসতে চান কবি, কিন্তু বাঘিনী কিছুতেই পেছন ছাড়ে
না, কিন্তু প্রতিবারই স্বপ্নে বাঘিনী তবু পিছু নেয়, তার চোখে তীব্র ফসফরাস,
সীমান্তের নদীটি পেরিয়ে সে অতর্কিতে সামনে আসে, দুই বাহু বাড়িয়ে কোলে তুলে নেয়।
তার করাল চুম্বনের দাঁত নখ ধীরে ধীরে বসে যাচ্ছে কবির গলায়। আবার পরের কবিতাতেই
জুয়েল কাতর হয়ে ওঠেন প্রেমিকার জন্য, প্রেমিকার দুটি চোখ একবার দেখার জন্য তার
বাড়ির পাশে দুপুরে কোকিল হয়ে বসন্তে গোপনে
এসে ডাক দেন।
‘দিওয়ানা জিকির’ বইটির
বিশিষ্টতাই হল কবিতাগুলোর ভাব, ভাষা ও চলনের বৈচিত্র। ‘ঈর্ষার এঞ্জিন’ কবিতাটির ভাষা
ও ছন্দ আরেকবার মুগ্ধ করে তার স্বকীয়তায়। এখানেও তৎসম শব্দের আধিক্য, কিন্তু তারই
পাশে আচমকা কিছু বিদেশি শব্দের ব্যবহার, মন্থর পয়ারের চলন এক অন্য জগতে নিয়ে চলে
যায়, এ কবিতা যেন মন্ত্রের মতো গম্ভীর, সুরেলা, ধ্রুপদ গানের মতো ক্লাসিক্যাল,
ঈর্ষার এঞ্জিন গরজি ওঠে
আজ; ঘুরছে মঞ্জুল মেঘাঙ্কুর;
ঘুম এক চিৎকার! আকাশে
চুনিলাল সূর্য-ক্রন্দন ঝরায় খুন।
উন্মাদ চায় তার অধরে
অনিবার স্বর্গবেশ্যার স্তনাগ্র।
কোন মনকির কোন নকিরে লিখে
মোর কোন সে-পাপ কোন অধর্ম?
............................................................................................................।।
আজ তোর স্কন্ধের গরিমা খ’সে
হায়! ছিন্নমস্তার তাথৈ নাচ!!
মনসুর হাল্লাজ জপেছে দমেদম
মাংসে মজ্জায় ‘আ’নাল হক’
ষণ্ডের তিন শিং খুঁজেছে
যোনিকূপ অন্ধ মুদ্গর আসন্ধ্যা
বল তোর উড্ডীন ডানাটি চাটে
কোন ধূর্ত জম্বুক মানিক মোর!
.......................................................................................
অসহায়তা বিপন্নতা জুয়েলের লেখায় বারবার এসেছে। তাঁর সামনে রুবিকন নদী, তিনি যেন
জুলিয়াস সিজার, এই নদী পার করলেই তাঁকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে হবে, তাঁর সামনে সেই পারলৌকিক
সেতু(পুলসিরাত), যেন তাঁর শেষ বিচারের দিন সমাগত, কেয়ামতের দিনের সেই অমানিশায় তিনি
একা, কিস্তিহীন, নিরশ্ব, রসদহীন, পিগমিদের চাইতেও ছোটো।
আর ওই থেকে-থেকে ফুঁসন্ত ব্লিজার্ড এক
আর এক আনক্যানি করাল হিমানী
আমাকে আদ্যন্ত ঘিরে আছে।
আবারও মোহিত হই, ‘আনক্যানি করাল হিমানী’, বিপন্নতার অনুবাদ এভাবেও করা যায়! তাঁকে
তাড়া করছে শতশত বল্মীকূট, লোম-কর্ণ শিবা, মেদুসা-মনসা আর কালী। উপমা ও রূপকের মাধ্যমে
বর্তমান সমাজকে এত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে খুব কমই দেখা যায়। আবার দেখি, এই অসহনীয়
বেঁচে থাকার মধ্যেও একমাত্র জেগে আছে প্রাণ। যে প্রাণ ‘অসীম হিম্মত লয়ে এক পায়ে’ খাড়া
হয়ে আছে। কে এই প্রাণ? সে হল মহাজীবন, সে কবির স্বপ্ন, সে কবির আশা,
আমি ফুঁ দিচ্ছি হাপরে আমার।
আমি আমাকে বলছিঃ ওঠো, জাগো!
………………………………………।
……………… আমি সাঁতরে চলেছি
আমার আয়ুর চেয়ে দীর্ঘ এক গন্ধকের নদী।
…………………………………………………………
আমি জয়ী হবো
আমি পার হবো রুবিকন!
‘সহোদরার জন্য একটি লাজুক টিট্টিভ’ কবিতায় পাই মরমীয়া মানুষকে। স্মৃতির টিট্টিভ
পাখি যাঁর অন্তরের জানালায় উঁকি দেয়, কামার্ত স্রোতে খসে যাচ্ছে মা-মেরীর বসন্ত-আঙরাখা,
ভগিনীর বসন্ত-আঙরাখা। আর দূরের ছায়াপথের খাঁজে খাঁজে শুধু ইশারার উপহার, তীব্র প্যাশন।
আর জুয়েল দেখতে পাচ্ছেন স্পর্শের বিদ্যুতে উড়ে যাচ্ছে এই পৃথিবী, টিট্টিভ পাখি তার
জিভ থেকে উগরে দিচ্ছে নীল বিষ। তবুও অবিচলিত মা-মেরী তাঁর তাঁত বুনেই চলেছেন, এদিকে
বারবার লুঠ হয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর বসন্ত-আঙরাখা।
মম প্রিয় বন্ধুগণ তপ্ত লাল শলাকা শানায়। আর
রক্তজবা কানে গুঁজে শব্দ করে ভয়ানক হাসে
মাঝেমাঝে বক্ষো’পরে বসে তারা
মোর পানে উঁচায় খঞ্জর।
আশির দশকের কবি-বন্ধুদের জন্য লেখা ‘মম প্রিয় বন্ধুগণ’ কবিতায় কি কবি জুয়েল মাজহার
একটু অভিমানী? বন্ধুর বেশে যারা আসে, আসে বিনোদক বাঁশি নিয়ে তারাই আবার সুযোগ পেলেই
বুকে উঠে খঞ্জর চালায়!
ঝড় শেষ হওয়া মানে
আকাশে রুপালি তাঁবু ফুলে উঠবে এখন আবার।
ধারালো নখের নিচে ঈগলেরা লুকায় শিকার।
আর তারা বিপুল ডানার তলে ছানাদের আগলে রাখে
সুকোমল লোমের আদরে।
…………………………………………………………
মিতব্যয়ী, সচেতন তারা জানে রসদ সামান্য, কিন্তু
সামনে আরো লড়াই লড়াই শুধু! লড়াই! লড়াই!
জুয়েল দেখেন আর আহত হন, পর্যুদস্ত
হন, কেননা যুদ্ধ আর খুনে লাল তরবারি দিয়ে তারা ক্রমাগত তাঁকেই শাসায়, আস্তিনের ভাঁজ
খুলে বের করে গোপন অস্ত্র, আর ঈশ্বরের প্রিয়তম ভেড়ার মতো প্রকাশ্য দিবালোকে তিনি বারবার
বলি হয়ে যান। নিজেরই কলবে তিনি কান পেতে শোনেন কোটি কোটি মার্জারের অবিরাম মরণ-চিৎকার।
ভীত জুয়েল পালিয়ে যেতে চান এই ভিড় থেকে, রেষারেষি থেকে, আর মধ্যরাতে বন্ধুরা কেবল তাঁবুর
ভেতর সংগোপনে খুমিশ ঢালছে পেয়ালায়।
‘ভিন্ন রণ-অভিজ্ঞতা হইতে আসি’ কবিতাটি
সম্পূর্ণ স্বাদের। সাধুভাষার প্রয়োগ এবং তীব্র, তীক্ষ্ণ শব্দব্যবহার এই কবিতাকে করে
তুলেছে একটি বিলম্বিত খেয়াল গানের মতো, পাঠকের মগজের কোষে কোষে যেন রুদ্রবীণার ঝংকার
তুলে দেয় এই কবিতা,
জানিও, রণদামামার ভিতর মুহুর্মুহু
যে জাগিয়া ওঠে
সে অন্য কেহ নহে সে আমি।
জানিও, যখন রণলিপ্ত তখন স্বজনহন্তা
আমি;
-কেননা ইহাই কর্তব্য আমার!
কেননা ক্ষত্রিয় আমি!
কখনও অর্জুন হয়ে তিনি বধ করে তাঁর
পরমাত্মীয়কে, তাঁর চোখ সজল হয়ে ওঠে, আবার পরমুহূর্তেই সচেতন হয়ে নিজের মধ্যে ফিরে আসেন,
এই তো কর্তব্য তাঁর – রণ-কর্তব্য। তিমি যে ক্ষত্রিয়, পাষানে রচিত। তবু তাঁর গ্রানিটে
নির্মিত হৃদয় ক্ষণকালের জন্য কেঁপে ওঠে কলিঙ্গের যুদ্ধের ময়দানে রাজা অশোকের মতো। আবার
তিনিই সদারিরংসু আর হননেচ্ছু,
তোমাদের জনয়িতা একমোবাদ্বিতীয়ম নিশানা
আমার;
আর ভক্ষ্য আমার অসীম ক্ষুধার!
আর, আমি তাহার দুশমন;
আর, সখাও তাহারই!
এক অদ্ভুত দোলাচল, অস্তিত্বের এক
আশ্চর্য সংকট তাঁকে পীড়িত করে,
আর জানিবে উভয়ের ক্ষেত্র একই – তাহার
আর আমার – তথাপিও,
উভয়ে ভিন্ন ভিন্ন রণ-অভিজ্ঞতা হইতে
আসি!!
এর আগেও বলেছি ‘দিওয়ানা জিকির’ বইটির কবিতাগুলির বৈচিত্র নিয়ে। ‘পাহাড়ে বেড়াতে
যাবার পর’ একটি গদ্যে লেখা কবিতা। এই ঘরানাতেও জুয়েলের কলম সমানভাবে সাবলীল। কয়েকটা
লাইন পড়ে দেখা যাক,
‘যখন পাহাড়ে যায় লোকে, ভালুকদের
কাছ থেকে তাদের ভারী চলনগতি আর যূথবদ্ধতার মন্ত্র শিখে নেওয়া ভালো……………বরফে, বক্ষবন্ধনীর
ভেতরে সেসব তুমি বহুদিন যত্নে রেখে দিও।‘
‘যেসব কান্নাকে এখন জড়ো করছি; আর ভাবছি, এঞ্জিন-রব আর খুরধ্বনি থেকে দূরেই রয়েছে
তোমা অভিজ্ঞান।তুমি এক লম্বা দৌড়; তুমি পত্রালির ভেতরে সাঁতার- বায়ূবাহিত বেলুনে বেলুনে।‘
‘…………………আর তাতে শব্দ করে ওঠে রাত্রি; -যেনো একাকী তক্ষক। যেনো ছল। এটুকু ছলই একদিন
আমাদের জোড়া ঠোঁটের কাছে প্রেম হয়ে আসবে কামের পেয়ালায়।‘
সবশেষে আবারও ফিরে
আসি ‘দিওয়ানা জিকির’ কবিতার কাছে। এমন সহজিয়া কথ্য ভাষায় এমন প্রেমের কবিতা
বাংলা-ভাষায় খুব কমই লেখা হয়েছে। এ কবিতা কোথায় যেন শুধুমাত্র কবির একার চাঁদলাগা
দিলের জিকির নয়, এ কবিতা সকলের, এ কবিতা পাঠকের ভাবনাজগতের ভেতরে এক নিজস্ব পৃথিবী
গরে তোলে, ঢেউ লাগে, চাঁদের গায়ে চাঁদ লাগে।
আমারে পড়বো মনে, জানি তুমি, ডাকবা আমায়
খাড়া-সোজা-উপ্তা হয়া দিওয়ানা জিকিরে অবিরাম;
এরপরই অভিমানী
জুয়েল বলেন, তিনি আর কোনোদিন ধরা দেবেন না, চলে যাবেন একা, খালেবিলে কিস্তি
ভাসিয়ে, যেন কনফুসিয়াসের স্বপ্নে বিভোর
কোনো চীনদেশী মানুষ। তিনি চুপ মেরে বসে থাকবেন কালেঙ্গাপাহাড়ের মতো, আর দেখবেন
তাঁর প্রিয়ার জিল্লতি। একা একা বসে তাস খেলবেন খেলার ছলে, তবুও শত আকুতি সত্ত্বেও
তাঁকে আর ফিরে পাবে না তাঁর প্রেমিকা। পথে বাদাড়ে তাঁর দিন কেটে যাবে, কেটে যাবে
গাছের আগায় বসে। তবু আর ফিরবেন না।
এই কবিতায় আশ্চর্য কিছু শব্দবন্ধ, যা একান্তভাবেই আঞ্চলিক,
কী অবলীলায় জুয়েল বসিয়ে দিয়েছেন, কবিতা কাব্যগুণ একফোঁটাও নষ্ট না করে। কিছু দেখে
নেওয়া যাক – হাইঞ্জাকালে, হাকালুকি হাওরে হাওরে, জিল্লতি,ফকিন্নির পোলা, উপ্তা
ডুবে, কুশার-খেতের ভিত্রে, পুটকিছিলা বান্দর, এসব শব্দ কবিতায় ব্যবহার করার জন্য
যে দক্ষতা লাগে, সেটা জুয়েলের কলম বারবার প্রমাণ করেছে।
আসলে কবিতার কোনও
ব্যাখ্যা হয় না। আমি বা আমরা পাঠ-প্রতিক্রিয়া রেখে যেতে পারি মাত্র। শুধু এইটুকু
বলি, যখন কোনও কবিতা কেবলমাত্র কবির একলার অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ না হয়ে সকলের আত্মা
ও হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত ছবি হয়ে ওঠে, তখনই সে কবিতা সার্থক। এটাও অবশ্য একেবারেই
আমার ব্যক্তিগত মত, আসলে ভালো লাগা, আর ভালো না লাগা, এই দুইয়ের মাঝখানের দোলাচলে
সব কবিকেই ভাসতে হয়,
উঞ্চা পথ, উঞ্চা কষ্ট
কান্ধে পাত্থর লইয়া উঠিতেছি আমি সিসিফাস!
(কান্ধে পাত্থর লইয়া)
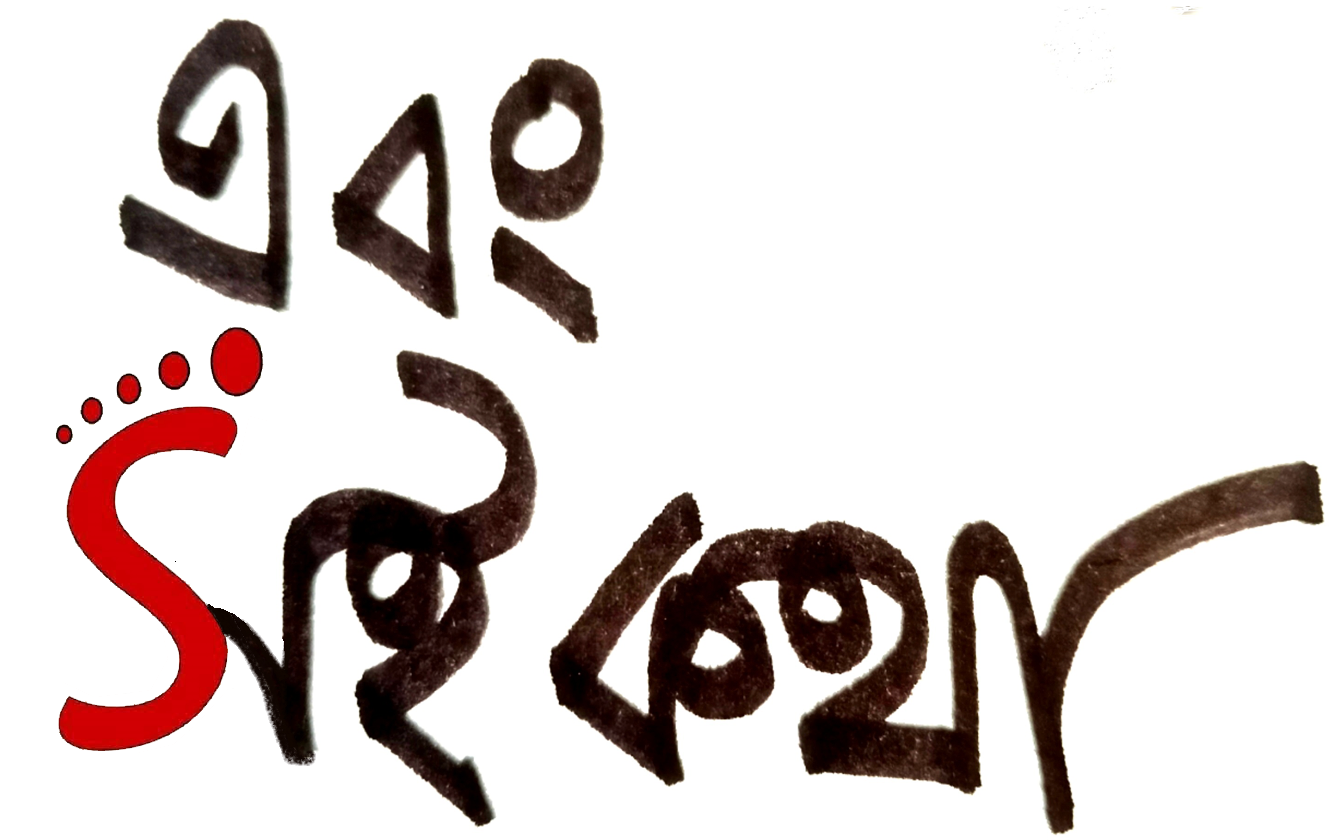



















0 মন্তব্যসমূহ