‘পথের পাঁচালী’- ফিরে দেখা ঘোরের বাকপ্রতিমা
‘স্মৃতির উদাস পথে ডেকে যায় সেলুলয়েডের
মমতায়; দৃষ্টিপথে একটি প্রকৃত গ্রাম হয়
আমার নিজস্ব চেনা আরেক পল্লীর সহোদর।
সেই কবেকার উপন্যাস ভিন্ন মাত্রা পায়, দেখি
গ্রাম্যপথে ওরা দুটি বালক বালিকা ছোটাছুটি
করে,ঘোরে কাশবনে,গহন
বর্ষায় ভেজে আর
শ্যামল মাটিতে কান পেতে শোনে ট্রেনের আওয়াজ
ঋদ্ধ সেলুলয়েডের সীমানা পেরিয়ে দুর্গা,অপু
খেলা করে চেতনার নীলিমায়।’ -- নান্দনিক সত্যের
পাঁচালি/ শামসুর রাহমান
একথা আমরা বহুদিন জেনে গেছি, সিনেমা, সাহিত্য, স্বপ্ন
এবং ব্যাপক অর্থে জৈবনিকতা পরস্পরের সমান্তরালে হেঁটে যাওয়া ভিন্ন
ভিন্ন সব ছায়াপথ, যারা একমাত্র মিলে যায় অনন্তের শেষে । সেই
কার্ডিনাল বিন্দুটিকে কখনোই ছুঁতে পারে না মানুষ, তবু তারই জন্যে আজীবন সিসিফাসদের পাথুরে পরিশ্রম জেগে থাকে,
হেরে যেতে হবে জেনেও ডঃ রিও লড়ে যায় অতিমারির বিরুদ্ধে, রক্তবমি করতে করতে ছবি আঁকেন সিফিলিস আক্রান্ত পল গ্যঁগা, একজন বিভূতিভূষণ লেখেন পথের পাঁচালী।
প্রকাশনা সংক্রান্ত তথ্য বলছে, সম্পাদক প্রথমে এই উপন্যাসটি ছাপতে চাননি, কারণ ওতে যথেষ্ট গল্প নেই। বিভূতিভূষণের সঙ্গে শর্ত ছিল, পাঠকের পছন্দ না হলে কয়েক কিস্তির
পর লেখাটির প্রকাশ বন্ধ হয়ে যাবে। অবশ্যই সে সব আশঙ্কা অমূলক প্রমাণ করেছিলেন
পাঠকরা, এবং ১৯২৯ সালে বই হিসেবে প্রথম প্রকাশিত হয় পথের পাঁচালী। যথেষ্ট গল্পের অভাব বলতে এক্ষেত্রে এটাই
বোঝাচ্ছে যে, এক্সপজিশন, রাইজিং
অ্যাকশন, ফলিং অ্যাকশন, ক্লাইম্যাক্স
শাসিত শিল্পের ক্লাসিকাল স্ট্রাকচারাল ড্রামাটিক কাঠামোর সঙ্গে এই বিশুদ্ধ বিবরণ
মূলক ধীরলয় উপন্যাসটির কাঠামোসম্পর্ক যথেষ্ট জটিল। এখানে গল্পের প্রত্যক্ষ শাসনের
বাইরে আদ্যোপান্ত ছড়িয়ে রয়েছে এক অন্যধরনের ন্যারেটিভ।
সত্যজিৎ আমাদের অনেকের মতো তাঁর ছোটবেলায় এই
উপন্যাসটি পড়েননি। শান্তিনিকেতনে থাকাকালীন এক পরিচিতের কথায় তিনি প্রথম এইটি পড়েন। তারপর যখন তিনি সিগনেট প্রেসের
‘আম আঁটির ভেঁপু’ বইটির প্রচ্ছদ আঁকছেন,
অলঙ্করণ করছেন, সেখান থেকেই ‘পথের পাঁচালী’ ছবি করার ভাবনা আস্তে আস্তে গেঁথে
যাচ্ছে তাঁর মাথার ভিতর। এখানে আর
একটি কথাও বলা থাক, সিগনেট-এর স্বত্বাধিকারী দিলীপকুমার
গুপ্ত শিল্পপাগল মানুষ, ক্যাটালিস্ট হিসেবে ছবিটি করার জন্যে তিনি নিরন্তর উৎসাহ জোগাচ্ছেন সত্যজিৎ রায়
নামের যুবকটিকে। যিনি ১৯৫০ সালে বদলি হবেন বিজ্ঞাপন সংস্থা জে ডি কীমারের লন্ডন অফিসে, এবং
লন্ডন পৌঁছে ঐইদিন সন্ধ্যায়ই দেখে ফেলবেন, ভিত্তোরিও
ডি-সিকার অমর সৃষ্টি ‘দি বাইসাইকেল থিফ’ । লুইজি
বার্তোলিনির উপন্যাস ‘বাইসাইকেল থিভস’কে ডি-সিকা যখন অনুবাদ করছেন চলচিত্রের ভাষায়, (দ্য বাইসাইকেল থিফ, ১৯৪৮) তিনি বেছে নিচ্ছেন এক নতুন চলচ্চিত্রভাষা
যাকে বলা হচ্ছে নিও রিয়্যালিজম ।
এখানে সাজানো সেট, আবেগমথিত সংলাপ, গতিশীল
নাটক কিছুই নেই। বরং বাস্তব জীবন থেকে নেয়া, ঘটনা ও মানুষের
চরিত্র চিত্রায়নের নিজস্ব উপস্থাপনা রিয়ালিজমের চূড়ান্ত মুহূর্তকে ভেঙেচুরে তৈরি করছে এক ধরনের ন্যাচারালিজম যা
প্রকৃত অর্থে ভিতর থেকে অগোছালো করে দিল ভারতীয় সিনেমার এতদিনের ইতিহাস।
আমরা পরে জেনেছি পথের পাঁচালী তৈরি করার জন্য, সত্যজিৎ কোন গোছানো চিত্রনাট্য তৈরিই করেন নি। পুরোটাই ছিল তাঁর মাথার ভেতর। আর কমিকস্ট্রিপের ঢঙে স্কেচবুকে আঁকা
হয়েছিল প্রায় পাঁচশো ছবি। কম খরচে, অনভিজ্ঞ, বলা ভালো বেশ কিছু নন প্রফেশনাল শিল্পীদের
নিয়ে তৈরি করা হয়েছিল এই সিনেমা। চলচ্চিত্রের
সঙ্গে উপন্যাসের বেশ কিছু জায়গায় আছে অমিল। গল্পের বেশ কিছু অংশ
হুবহু তুলে ধরেননি সত্যজিৎ। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় উপন্যাসের শুরুর দিকেই গ্রামের
মন্দিরে সকলের সামনেই ইন্দির ঠাকরুণের মৃত্যু ঘটে। তা দিয়েই পথ চলা শুরু কাহিনীর । কিন্তু চলচ্চিত্রে অপু ও দুর্গা তার মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে বেশ পরে। বর্ষায় ভিজে প্রচণ্ড জ্বর
বাঁধিয়ে দুর্গার মৃত্যু ঘটে বলে চলচ্চিত্রে দেখানো হয়েছে । তবে
উপন্যাসে মৃত্যুর কারণ অজানা। হরিহর রায়ের পরিবারের গ্রাম ত্যাগ দিয়ে চলচ্চিত্র
শেষ হলেও উপন্যাস কিন্তু সেই ভাবে শেষ হয়নি।
সত্যজিতের জন্ম শতবর্ষে পথের পাঁচালীকে আরও একবার
ফিরে দেখতে গিয়ে আমার এই কথাগুলি মনে এল। যে সিনেমাটি আমাদের বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রয়ে গেছে সর্বক্ষণ, তার কাছে ফেরত যাওয়ার পথে তাকে নিয়ে নানা বিশ্বাস ও তর্কের একটা পুনর্দর্শনও খুব জরুরী। আগেই বলেছি, এই প্রথম ভারতীয় চলচ্চিত্রে আমরা দেখলাম নিখাদ বাস্তবতার প্রতিলিপি, পরিণত রিয়ালিজম, সাহিত্য বা নাটকের দাসত্বমুক্ত বিশুদ্ধ চলচ্চিত্রের ভাষা। ঠিক কি অর্থে
কথাগুলো আমার মনে হল বলছি।
বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' আমাকে
ছোটবেলায় শিখিয়েছে 'দেশ' মানে পতাকা আর ম্যাপ নয়, দেশ মানে ছাপ্পান্ন ইঞ্চির চিৎকৃত আস্ফালন বা কোন দিদি-দাদার
অনুপ্রেরণার পোস্টারে হাসিমুখের ছবি নয়। ঘরের হাঁড়িকুড়ি, নারকোল মালা, রাংতা থেকে ঘাস, জল, মাঠ, বন, ভাঁটফুল পরিব্যাপ্ত এক সংসার। সেখানে শঙ্খমালা কিশোরীরও করুণ চাল ধোয়া হাত
জেগে থাকে সমান মমতায়।
সাহিত্যের বিশুদ্ধতা নয়, বরং সত্যজিতের ‘পথের পাঁচালী’ পরে আমাকে শেখাল চলচ্চিত্রভাষার সঙ্গে সাহিত্যভাষার এক পুনরাধুনিক
আত্মীয়তার কথা। আমরা দেখলাম কোনও বিশেষ জীবনের বাস্তবতা সটান এ ছবির শরীরে প্রবেশ
করেনি। বরং বলা চলে এ
ছবি ‘পুনরাবিষ্কার’ করেছে এমন এক
বাস্তবতাকে, যা বিভূতিভূষণের উপন্যাসে শুধু কেলাসিত আকারেই
মূর্তি পেয়েছিল। তাই এই সিনেমাটি শুধু উপন্যাসের বিষয়টির পুনর্কথন নয়, বরং এক বিশেষ প্রতিবেশের আঙ্গিককে ছবির শরীরে তুলে আনার আয়োজন।
সত্যজিৎ কোথাও লিখছেন, কাহিনীতে আবশ্যিক নয়, জরুরী নয়, এমন কোনো বস্তুর ছবিতে স্থান নেই। খুব সুন্দর কোনো দৃশ্য হাতে আছে, তাই তাকে ছবিতে রাখতে
হবে, ওস্তাদ ছবি করিয়ে এমন বিলাস করতে পারেন না। যুক্তিবাদী
ছবির এটাই প্রধান যুক্তি, যে আখ্যানের ব্যাকরণে কোনও
বিশৃঙ্খলা থাকতে পারবে না। কিন্তু ‘পথের পাঁচালী’তে শুধু কি এই কাহিনীর
চলনটিই পাচ্ছি ? নাকি ন্যারেটিভের সংহতির মধ্যেই ক্রমাগত
ঢুকে পড়ছে এক বিবরণ, সরাসরি কাহিনীতে যার তেমন বিশেষ অবদান
নেই ? এটাই হয়তো এক ধরনের মন্থর অলস লয়কারীর স্টাইল, যার কোনো আপাতলক্ষ্য নেই।
সত্যজিৎ নিজে একে বলেছেন ramble, বলছেন ছবি করার সময়ই তিনি জানতেন উপন্যাসের এই ইতস্তত
মন্দ চলন তাঁকে অনেকটা
ধরে রাখতে হবে; ‘life in a poor Bengali village does ramble’ (‘a long
time on the Little Road’)। তাঁর ‘পথের পাঁচালী’তে আমরা কখনও শুধু দেখছি দিন বা ঋতুর
আবর্তন, দেখছি দিনের উত্থান-পতন, স্রেফ
সময় বয়ে যাওয়া, আর কিছু নয়। ঘটনা থেকে, চরিত্র থেকে কিছুটা তফাতে
দাঁড়িয়ে আমরা দেখছি এই প্রবাহকে। যেখানে এক একটা দীর্ঘ দৃশ্যের বিষয় হয়ে উঠছে সময় নিজেই। সেই মুহূর্তে ‘পথের পাঁচালী’ আর অপু-দুর্গা-সর্বজয়ার গল্প থাকছে না,
হয়ে উঠছে দেশ নামে আমার এক বিশুদ্ধ পৃথিবীর সাক্ষ্য। সেখানকার
নিসর্গের, আলো, হাওয়া, বৃষ্টির আসা-যাওয়ার, শরীর ধারণের গল্প।
সত্যজিৎ সরাসরি উপন্যাস থেকে তুলে আনেননি এই কৌশল, বরং নিজস্ব চলচ্চিত্রভাষায় একে নির্মাণ করেছেন, বানিয়েছেন এক
চরিত্রকেন্দ্রিক গল্প, যেখানে, ব্যক্তি
চৈতন্যের বিবর্তনের কাহিনীকে অতিক্রম করে গভীরে স্পর্শ করা যায় পরিবেশকে। পরিবেশ
তখন আর শুধু পটভূমি থাকে না, তার উপস্থিতি হয়ে ওঠে জীবন্ত,
ইন্দ্রিয়ময়। গল্পের প্রত্যক্ষ দাবিকে কিছুটা দূরে সরিয়ে ডিটেল-এর
অন্যরকম ব্যাবহার করছেন দুজনেই। ঘরের নিত্যব্যবহার্য অস্তিত্ব থেকে শুরু করে,
মাঠ, বন পরিব্যাপ্ত এক গ্রামদেশের অনুপুঙ্খ
তৈরী করছেন, যাকে ঘিরে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে দৈনন্দিনের সাধারণ
প্রতিলিপি। নিত্যবৃত্তের নথিভুক্তি
এক দিকে যেমন ছুঁয়ে যাচ্ছে সময়ের বৃত্তকে, প্রকৃতিকে,
অন্য দিকে তেমনই ছুঁয়ে আছে ইতিহাসবই-এ বাদ পড়ে যাওয়া, বৃহৎ আখ্যানে ধরা না পড়া এক
সাধারণ যাপনকে। শুধু কাল বা টাইম নয়, এই বিবরণে ক্রমশ শরীর
ধারণ করছে স্পেস বা
স্থানও। এখানে একাধিক অর্থে রূপ ধারণ করছে সেই দেশ, যে দেশ
দেশাত্মবোধের উচ্চারণে পাওয়া যায় না। রিয়ালিজমের গ্রন্থিগুলো আলগা করে ন্যাচারালিজমের সঞ্চার আমাদের দেখিয়ে
দিচ্ছে, দেশপ্রেমের শৃঙ্খলার বাইরে আর এক নতুন দেশের আবিষ্কার। এই ঘটনাহীন, নাটকহীন
মন্থর যাত্রায় সময় শুধু আর আধার হয়ে নেই, সে ঘন হয়ে উঠছে,
শরীর ধারণ করছে। এখানে
টানটান ঘটনার ঘনঘটা নেই, কিন্তু
নিরুচ্চারে বলা একটা জীবনযাপনের নকশা রয়েছে। রয়েছে অর্থনৈতিক পরিচয়, সমাজচিত্র, বৈষম্য ( এক অলৌকিক তারসানাইয়ের সঙ্গে
সঙ্গে অপু দুর্গাকে বঞ্চিত করে চলে যাচ্ছে মিষ্টিওলা) সবই বোনা রয়েছে নকশার টানাপোড়েনে। কিন্তু, দিনলিপির ছন্দ
থেকে তা কোনোভাবেই বিচ্যুত নয়, লাউড বা তীব্র নয়, নিসর্গ থেকে আলাদা কোন ইতিহাসও নয়। বরং অস্বাভাবিক রকম
স্বাভাবিক।
একটি বিশেষ অবলোকনকে প্রতিষ্ঠা করছে এই সব দৃশ্য, যা দৃশ্যর সঙ্গে এক হয়ে দেখা, সমাজতাত্ত্বিক
চিত্রায়ণের রীতি তেমন মানতে রাজি নয়। আব্বাস কিয়ারোস্তামির ছবির কথা বলতে গিয়ে
দার্শনিক জঁ-লুক ন্যান্সি একে বলেছেন ‘চলচ্চিত্রের সাক্ষ্য’ (The Evidence of Film, Abbas Kiaarostami,
2001) যা দিনযাপনের সাক্ষ্য থেকে খুব একটা আলাদা কিছু নয়। আমরা তাই এই সিনেমাটিতে চার দিকে ব্যাপ্ত অখন্ড এক অস্তিত্বের মানচিত্র দেখছি। আমাদের
চোখের সামনে একটা সময়, অঞ্চল, প্রতিবেশ
ক্রমশ অবয়ব ধারণ করছে।
ধ্রুপদি রিয়ালিজম দাবি করে পরিচালক নিজেকে সম্পূর্ণ
সরিয়ে রাখবে কাহিনী থেকে, ক্যামেরা
লুকিয়ে রাখবে নিজের উপস্থিতি। জিমি-জিব খুঁজে নেবে না কোন অলৌকিক আকাশমুখী
অ্যাঙ্গেল। কিন্তু ‘পথের পাঁচালী’ ফিরে দেখতে দেখতে আমি মাঝে মাঝেই অনুভব করছি যেন এক ন্যারেটরের
নিঃশব্দ প্রবেশ। কে যেন নীরবে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী দিয়েই বর্ণনা করছে এইসব
চরিত্রদের, যেখানে তাকে ডি কন্সট্রাকশনের কোন সুযোগই নেই।
কাশবনের দৃশ্যে সে
উপস্থিত, বৃষ্টির দৃশ্যে সে কথা বলছে আমার সঙ্গে। হরিহর ও সর্বজয়ার সন্ধ্যার চিত্রমালায় একটু
খেয়াল করলেই টের পাওয়া যাচ্ছে
তার উপস্থিতি।
ইন্দির ঠাকরুণের দাওয়া ঘিরে
ঝিঁঝি-ডাকা প্রাণস্পন্দিত অন্ধকারে তাকে অনুভব করছি আমি। সন্ধ্যার আসরের শুরুতে ধীরে ক্যামেরা এগিয়ে গিয়েছিল হরিহর আর অপুর ওপর, একেবারে শেষে ঠিক একই পথ ধরে পায়ে পায়ে পিছিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। আমার
সঙ্গে কে যেন একটু তফাতে দাঁড়িয়ে দেখছে এক গৃহস্থের দিনান্তের মন্থর সব মুদ্রা, খুচরো কথা, নিতান্ত প্রাত্যহিক অভ্যাস।
এরপর একটি ব্যক্তিগত অবলোকনে আসি, আমার চোখে সত্যজিত একজন আদ্যন্ত মিউজিক্যাল ফিল্ম ডিরেক্টর
যদিও পথের পাঁচালী একটি মিউজিক্যাল ফিল্ম নয়। ব্যাপারটা একটু অস্পষ্ট, বা সুপারফিশিয়াল লাগতে পারে। কিন্তু দীর্ঘ সময় ধরে তাঁর চলচ্চিত্রভাবনাকে অনুসরণ করলে এই কথা মনে আসা স্বাভাবিক। মিউজিকের ইনফ্লুয়েন্স তাঁর প্রতিটি ছবিতে খুবই বেশী। যদিও তিনি গুগাবাবার মত মিউজিক্যাল ছবি পরে অনেক করেছেন,
আমি বলতে চাইছি পথের পাঁচালীরও একটা নিজস্ব সাংগীতিক কাঠামো আছে। এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে সত্যজিতের মিউজিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ডটা
মূলত পাশ্চাত্য সংগীতের হাত
ধরে। এবং নিজস্ব সাংগীতিক অনভিজ্ঞতার কারণেই তিনি রবিশঙ্করের হাতে তাঁর এই ছবির
সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব
তুলে দিয়েছিলেন।
আমরা জানি সঙ্গীতের কাঠামো আর ফিল্মের কাঠামোর মধ্যে, প্রধান
সংযোগের সুত্রটা হচ্ছে ‘সময়’। দুটো শিল্পমাধ্যমই একইসঙ্গে
সময়ের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে কিন্তু একটি অনিবার্য পার্থক্যও এখান
থেকেই তৈরি হয়ে ওঠে। সাধারণত একটা
মিউজিকাল পিসকে সময়ের অভিজ্ঞতাটায় নিয়ে যেতে কোনো গল্প বলতে হয় না। কিন্তু
ফিল্মের ক্ষেত্রে গল্পটার উপরেই ডিরেক্টরকে মূলত নির্ভর করতে হয়। তাই
ব্লেন্ডিংয়ের ক্ষেত্রে এখানে একটা বড় পার্থক্য তৈরি হয়ে যেতেই পারে। আবার একই সঙ্গে, সঙ্গীতের ছন্দটা পুরোটাই যেমন শ্রাব্য, শ্রুতি নির্ভর, চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে সেটা গোটাটাই দৃশ্যনির্ভর। এখানেও একটা জরুরী পার্থক্য তৈরি হচ্ছে। তাই দুটো বিষয়, তাই এক হলেও বেশ আলাদাও বটেই। সংগীত সম্পূর্ণ বিমুর্ততায় তৈরী হতে পারে,
কিন্তু ফিল্মের ক্ষেত্রে এই বিমূর্ততাটা গল্প বলার আর্টের মধ্যেই
সীমাবদ্ধ রাখতে হয়। সঙ্গীতের কাঠামোটা প্রয়োগ করে আসলে
আমরা গল্প বলাটাকেই সমৃদ্ধ করতে পারি মাত্র। আর রবিশঙ্কর ঠিক সেই কাজটাই করেছিলেন মূলত বিভিন্ন রাগের ছোট ছোট পিসকে বিভিন্ন ভারতীয়
তারযন্ত্র বা স্ট্রিং ইন্সট্রুমেন্টের ব্যবহারে সীমাবদ্ধ রেখে।
এটা বোঝা যাবে ইন্দির ঠাকরুণের চরিত্রে চুনিবালা
দেবীকে দিয়ে গান করানোর ঘটনায়। ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় প্রখ্যাত সংগীত বিশেষজ্ঞ ও
লেখক সুধীর চক্রবর্তীকে
সত্যজিত বলেছিলেন, ‘চুনিবালা দেবীকে যেদিন প্রথম তাঁর পাইকপাড়ার বাড়িতে দেখতে যাই, সেদিনকার মনের অবস্থা ভোলবার নয়। ছবির
কাজ শুরু হয়ে গেছে। অপু, দুর্গা,
হরিহর, সর্বজয়ার ভূমিকা নির্বাচন হয়ে গেছে।... বাকি আছে কেবল ইন্দির ঠাকরুন।
চুনিবালা আমাদের হতাশ করলেন না। ‘পঁচাত্তর বৎসরেরে বৃদ্ধা,
গাল তোবড়াইয়া গিয়াছে, মাজা ঈষৎ ভাঙিয়া শরীর
সামনে দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে’.... বর্ণনার সঙ্গে অমিল হলো না।
জিজ্ঞেস করলাম- আপনি ছড়া জানেন কোনো? আবৃত্তি করতে পারেন ? ‘ঘুমপাড়ানি
মাসি-পিসি’ ছড়ার দশবারো লাইনের বেশি আমি কখনও শুনিনি।
চুনিবালার মুখে এর পরিসর বৃদ্ধি হল আশ্চর্য ভাবে।.... শ্রদ্ধা হোল প্রবীণার
স্মরণশক্তি দেখে।
চুনিবালা’র অনেক গুণের মধ্যে তাঁর গলাটি আবিষ্কার হয় বেশ পরের দিকে। এক দিন
সুটিং-এর শেষে হরিহরের দাওয়ার বসে বৈকালিক চা-পানের সময় তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম,
আপনি গান জানেন ? উপন্যাসে বা চিত্রনাট্যে
ইন্দিরের গানের উল্লেখ ছিল না, তবে কদিন থেকেই মনে হচ্ছিল,
ইন্দিরের কোন অলস মুহূর্তে তাঁর গাওয়া একটি গান দিতে পারলে মন্দ হয়
না।
চুনিবালা তখন বলেছিলেন- “ধর্মমূলক চলবে কি ?” সত্যজিৎ রায়
বলেছিলেন, চলবে। তখন চুনিবালা দেবী ওরফে কাহিনীর ইন্দির ঠাকরুন গেয়েছিলেন- “মন আমার হরি
হরি বল/ হরি হরি হরি বলে/ ভবসিন্ধু পার চল”। গানটি রেকর্ড হয়েছিল, কিন্তু সিনেমায়
ব্যবহার হয়নি। তার বদলে আমরা ইন্দির ঠাকরুণকে অন্য গান গাইতে শুনেছি।
সেই ঘটনাক্রমটি এ রকম – সেদিন চাঁদনি রাত। দাওয়ার
পশ্চিম দিকে মুখ করে হাতে তাল রেখে ইন্দির ঠাকরুন গান করছেন। এমন দৃশ্যটা যখন
ওপরের গানটি সহ তোলা হবে তখন শট নেওয়ার কিছুক্ষণ আগে চুনিবালা দেবী বললেন, তাঁর আরেকটা গান মনে পড়েছে। সেটা নাকি আরও ভালো। চুনিবালা
সত্যজিৎবাবুকে প্রশ্ন করলেন, “শুনবেন ?” শুরু হল তাঁর গান। “হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হল/ পার কর আমারে”। সুধীর
চক্রবর্তীর বয়ানে “ফিকিরচাঁদি
পর্যায়ের চমকপ্রদ গানখানি চুনিবালা দেবীর স্মৃতির সরণি বেয়ে অবিনশ্বর হয়ে গেল
বিশ্বশ্রেষ্ট চলচ্চিত্রে ।”
ইন্টারনেট স্যাভি, ইউটিউব ও নেটফ্লিক্সের ওটিটি প্ল্যাটফর্মে দুরস্ত, টেকনোলজির
প্রসাদপুষ্ট আমরা প্রতিদিন ভুলে চলেছি, এই দেশে গতবছর লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ হাজার
হাজার কিলোমিটার পথ হাঁটতে হাঁটতে ফিরে এসেছে গত লকডাউনে। ভ্যাকসিনের লাইনে হাহাকার করছে মানুষ, ডাক্তার
ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মুখ কখনো না দেখা করোনা আক্রান্ত মানুষ পোকা মাকড়ের মত মরে
যাচ্ছে, বেঁচে থাকছে। বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালী উপন্যাস এবং
সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালী চলচ্চিত্রটি, আমাকে ফিরে দেখাল, এই দুটিই আসলে, নিও রিয়্যালিস্ট শিল্পভাষায় লেখা
এইসব চেনাঅচেনা মানুষেদেরই বাকপ্রতিমা।
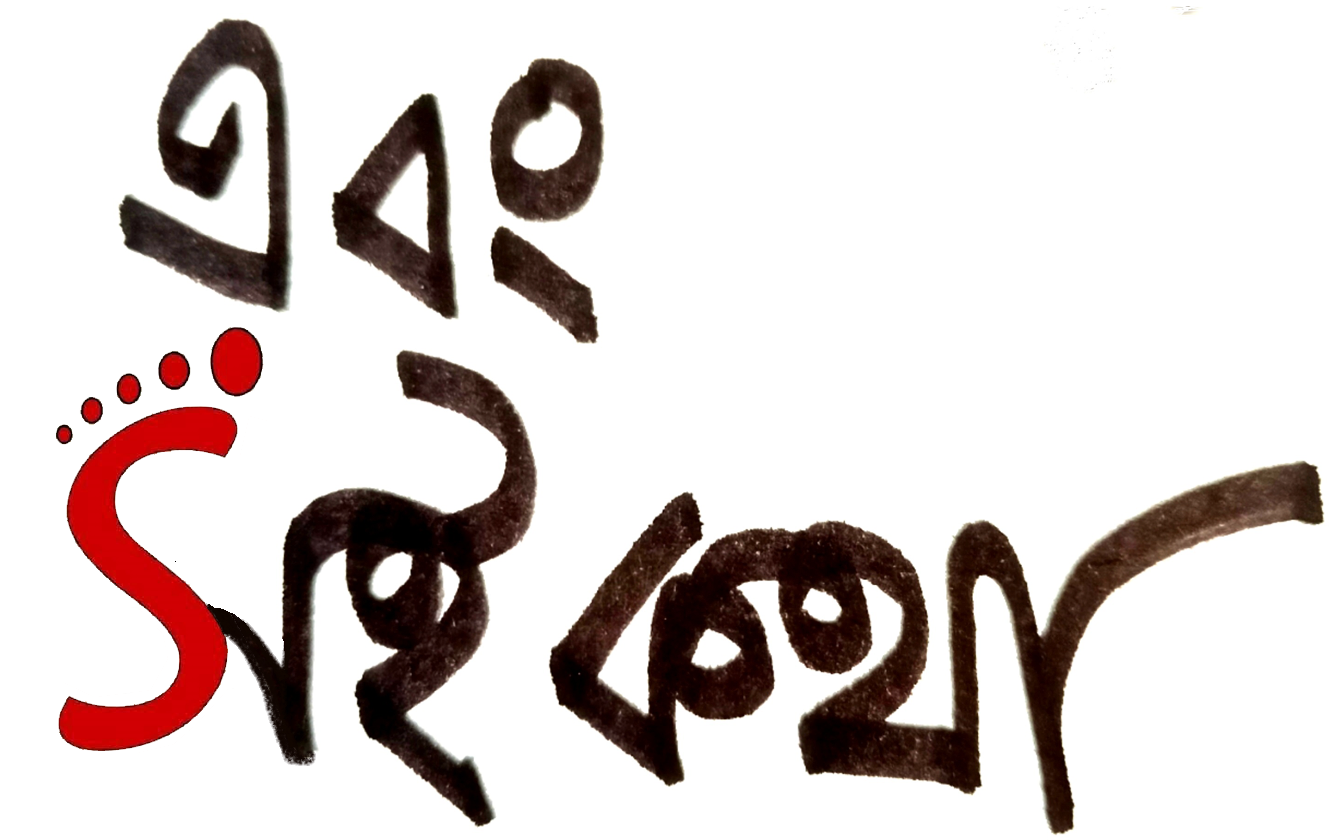


















0 মন্তব্যসমূহ